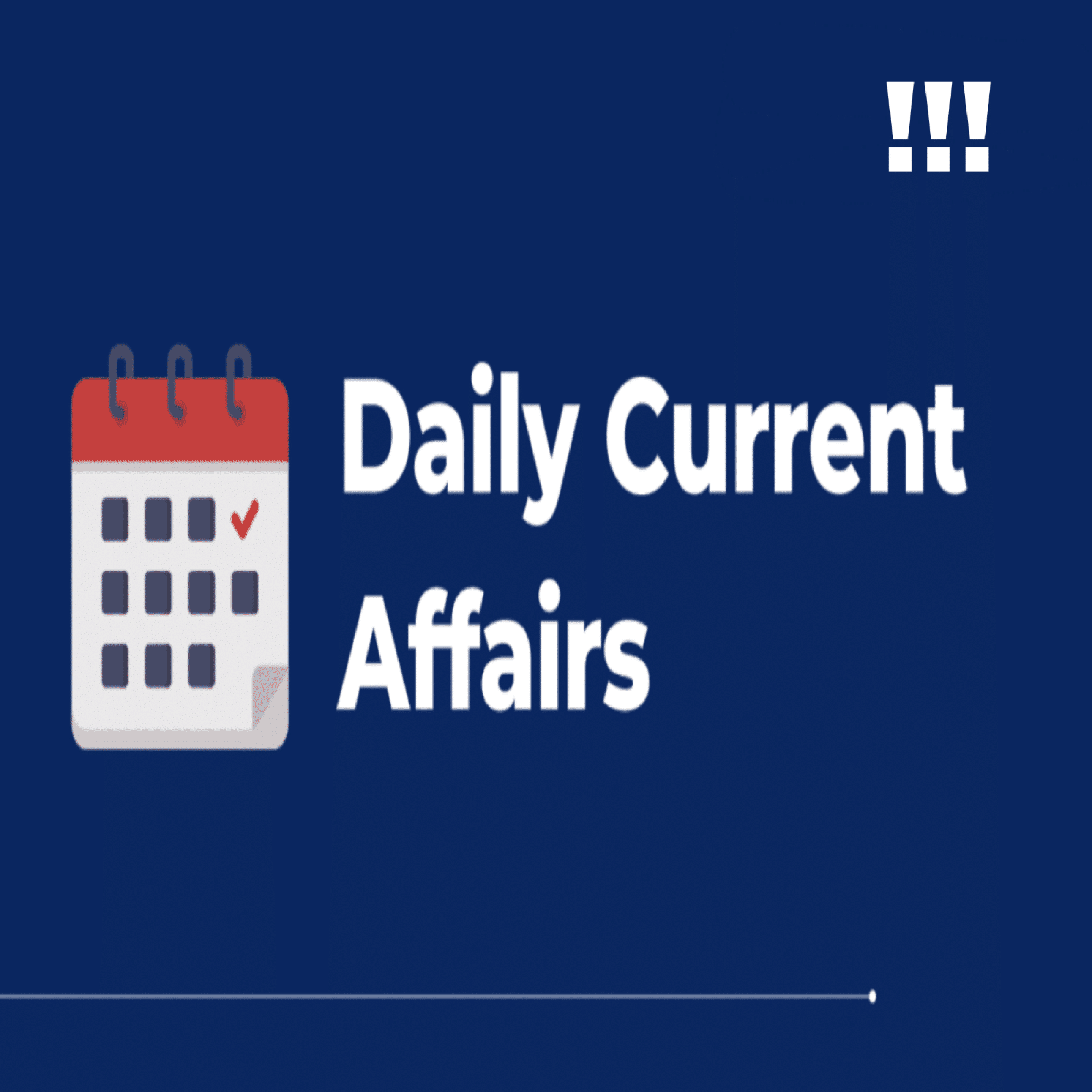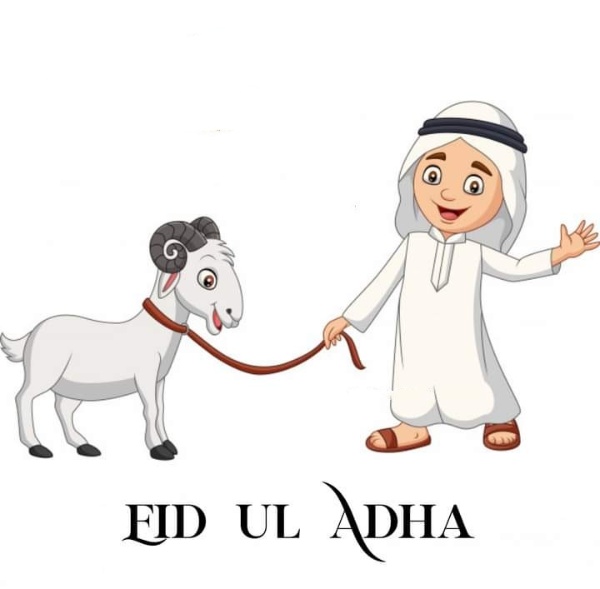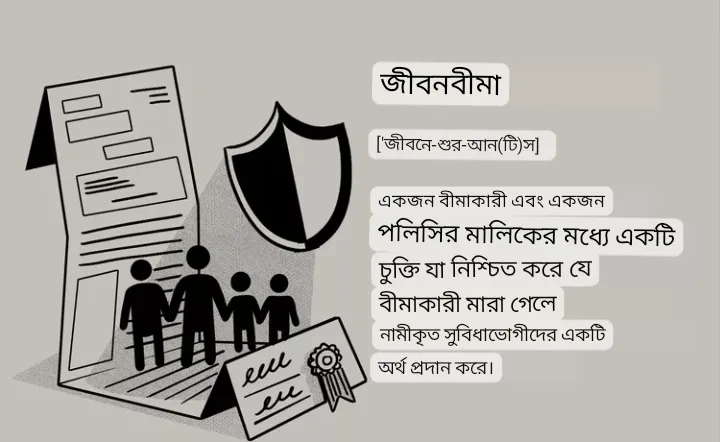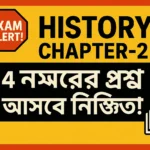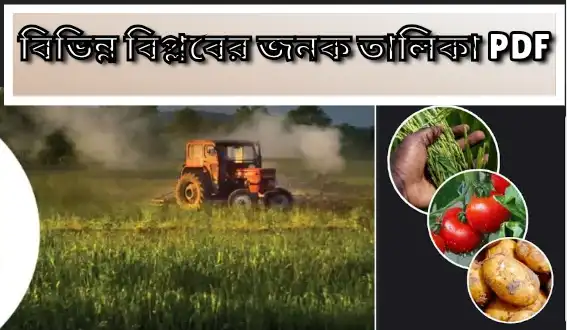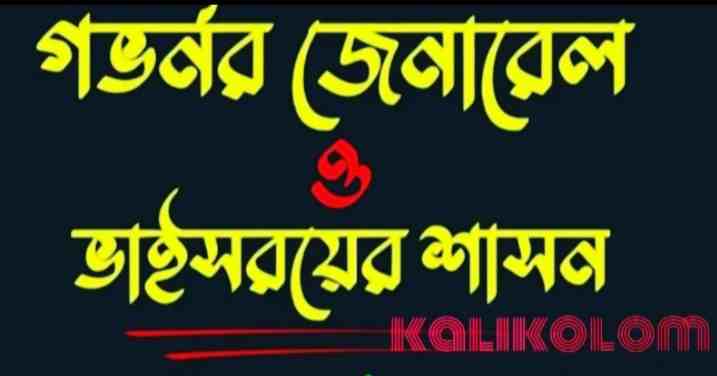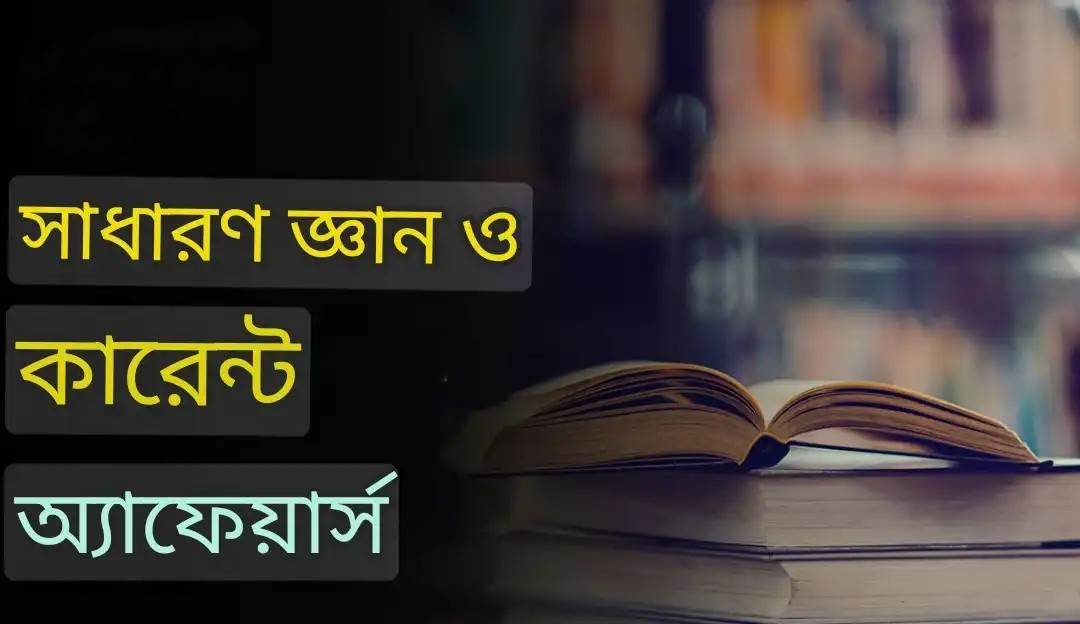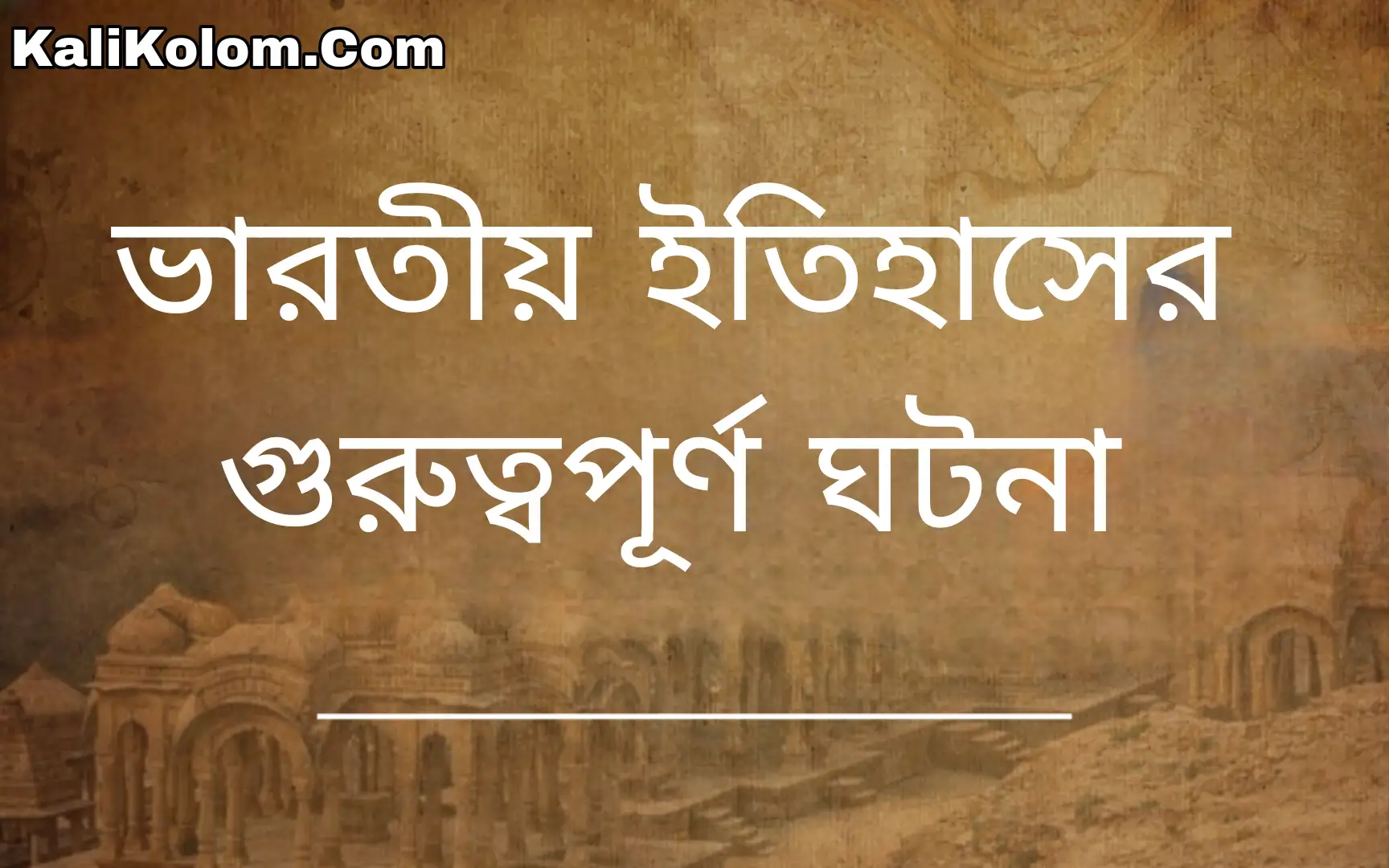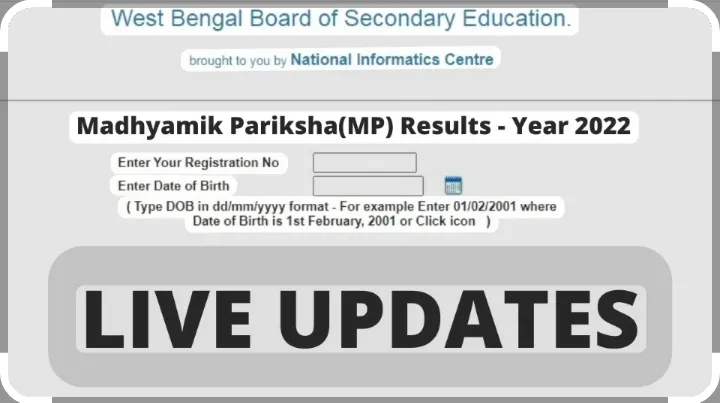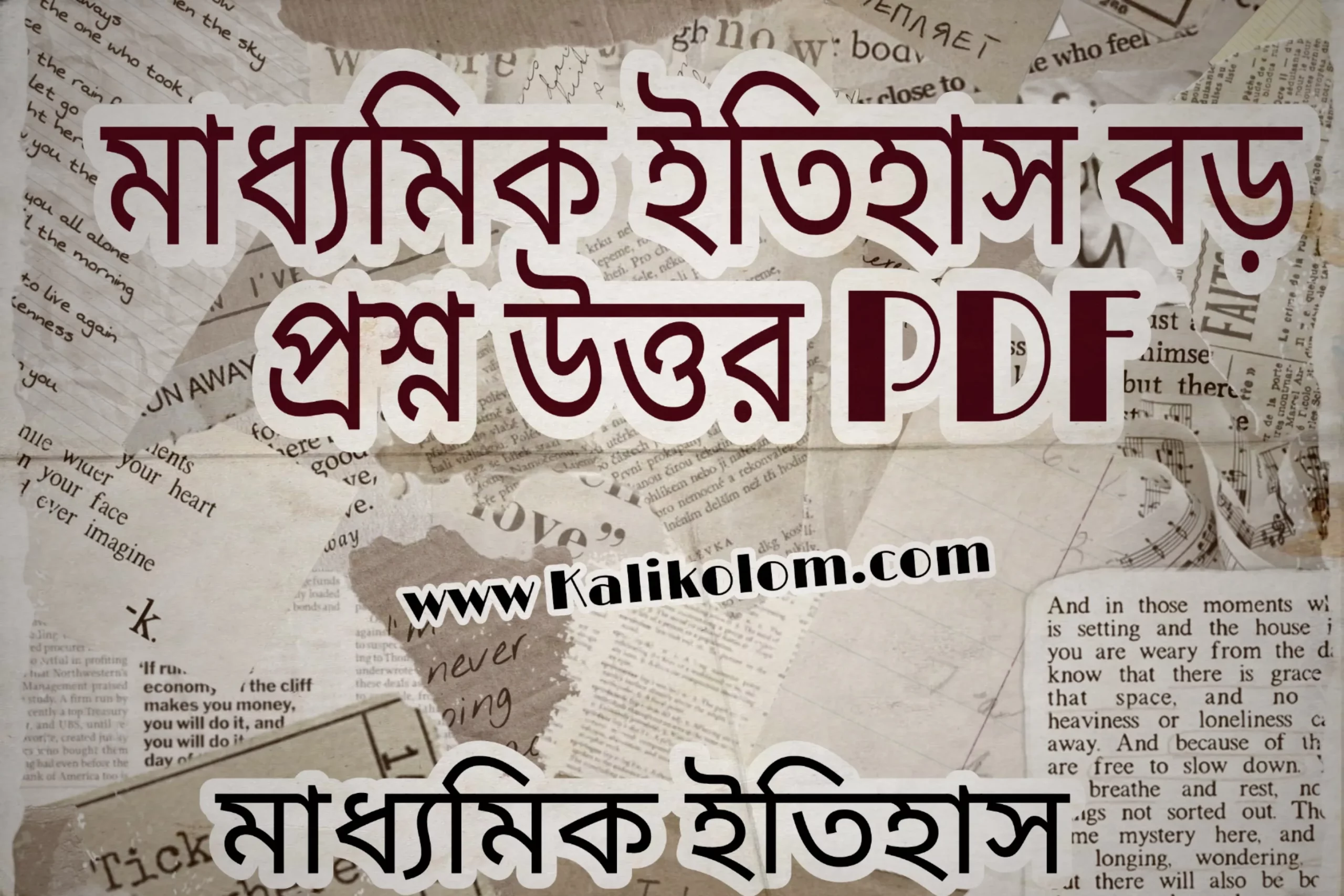চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
লর্ড কর্নওয়ালিশ ভারতে স্বল্পমেয়াদি বন্দোবস্তের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রস্তাব রাখেন। ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তা অনুমোদন করলে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ বাংলায় দশসালা বন্দোবস্তের পরিবর্তিত রূপ হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে স্থির হয়, সর্বোচ্চ নিলামদাতাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে। জমিদাররা নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বংশানুক্রমে জমি ভোগদখল করবেন। জমিদার জমি হস্তান্তরের অধিকার পাবেন। নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব মেটাতে ব্যর্থ হলে ‘সূর্যাস্ত আইন’ অনুসারে সাকার উক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে পুনরায় নিলাম ডেকে বঙ্গোবস্ত দিতে পারবেন।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল
লন্ডনের পরিচালক সভা আশা প্রকাশ করে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে এবং কৃষকশ্রেণি সুখ ও সম্পদের অধিকারী হবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুত চিরস্থায়ী ব্যবস্থার কিছু তাৎক্ষণিক সূফল ছিল এবং এর ফল ভোগ করেছিল বিদেশি ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদার কিছু বিত্তবান জমিদার। কিন্তু কুফলের মাত্রা ছিল অনেক বেশি। আর সেই ভার বহন করতে হয়েছিল মূলত বাংলার কৃষক সমাজকে।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল:
এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল। মার্শম্যান বলেছেন, “It was a bold, brave and wise measure” এই ব্যবস্থার ফলে –
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:
(i) সুনির্দিষ্ট রাজস্বনীতি: রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ ও তা আদায়ের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়।
(ii) আয়ব্যয়ের হিসাব: রাজস্ব আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ফলে সরকারের পক্ষে আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা সহজ হয়। তারা নানা সংস্কারমূলক কাজেও মনোযোগী হন। ও সামাজিক ক্ষেত্রে জমির স্থায়ী মালিকানা: স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা পাওয়ার ফলে কোনো কোনো জমিদার জমির উন্নতি করার উদ্যোগ নেন।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল:
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল অপেক্ষা কুফল ছিল অনেক বেশি।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:
(i) অধিক রাজস্ব হার: জমি জরিপ না করে এবং জমির গুণাগুণ বিচার না করেই রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করা হয়েছিল। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজস্বের হার ছিল বেশি।
(ii) কৃষকদের দুরবস্থা: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল কোম্পানির সঙ্গে জমিদারদের। এই বন্দোবস্তে কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কর্নওয়ালিশ আশা করেছিলেন যে, জমিদাররা স্বেচ্ছায় কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু জমিদাররা কৃষকের ওপর ইচ্ছামতো রাজস্ব চাপিয়ে দেন এবং খেয়ালখুশিমতো কৃষকদের জমি থেকে বিতাড়িত করতে শুরু করেন। এইভাবে কৃষকশ্রেণি দুরবস্থার শেষ সীমায় এসে পৌঁছোয়।
সামাজিক ক্ষেত্রে:
(i) জমিদারির অবসান: জমিদার নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব জমা না দিলে ‘সূর্যাস্ত আইন-এ জমি বাজেয়াপ্ত করে তা নিলাম করা হত। এর ফলে বহু বনেদি জমিদার তাঁদের মারি হারান।
(ii) নব্য মহাজনদের অত্যাচার: স্থায়ীভাবে জমির মালিক হওয়ার লোভে বহু শহুরে মহাজন, বণিক নিলামে জমিদারি কিনে নো। ইতিহাসবিদ তারাচাঁদ-এর মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বর্তনের ফলে গ্রামের চিরাচরিত সমাজ-সংগঠন ভেঙে পড়ে এবং নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। তাদের সঙ্গে গ্রামীণ জীবন বা কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো পরিচয় ছিল না। স্বভাবতই কৃষকের সমস্যা তারা অনুধাবন করতে পারেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল যে-কোনো উপায়ে প্রচুর রাজস্ব আদায় করা। এইভাবে বাংলার কৃষক সমাজ নব্য মহাজনি-জমিদারের শিকারে পরিণত হয়।
(iii) কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত: সরকার ১৭৯৯-এ ৭ নং রেগুলেশন জারি করে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম চাষিদের জমি থেকে উৎখাত করার অধিকার জমিদারদের হাতে তুলে দেয়। এই আইনের সুযোগে জমিদাররা সামান্য কারণে বহু কৃষককে উৎখাত করে। তাই সিরাজুল ইসলাম এই আইনকে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম কালাকানুন বলে সমালোচনা করেছেন।
(iv) মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব: বর্ধমানের জমিদার তেজচন্দ্র সহজে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর জমিদারিকে ছোটো ছোটো ভাগে বিভক্ত করে অন্যের কাছে বন্দোবস্তু দিয়ে দেন, এই ব্যবস্থা ‘পত্তনি’ নামে পরিচিত। পত্তনি আবার তার অংশকে আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে অন্যের কাছে বন্দোবস্ত দেন, এদের বলা হত ‘দরপত্তনিদার’। এইভাবে জমিতে একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব ঘটে। পুলিশ সুপার ডাম্পিয়ার মন্তব্য করেছেন যে, জমির বিভিন্ন স্তরে উপস্বত্ব সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলি নিষ্পেষিত बी হচ্ছে।
(v) কৃষির বাণিজ্যকরণ: অতিরিক্ত রাজস্বের চাপে জর্জরিত কৃষকশ্রেণি মহাজনের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। ঋণ-ফেরত নিশ্চিত করার জন্য মহাজনরা কৃষকদের অর্থকরী ফসল, যেমন—নীল, পাট, তুলো ইত্যাদি চাষ করতে বাধ্য করে। এইভাবে কৃষির বাণিজ্যকরণ (Commercialisation of Agriculture) ঘটে। পরিণামে কৃষকের খাদ্যাভাব প্রকট হয়।
মন্তব্য:
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের পক্ষে ছিল ক্ষতিকারক। কৃষকদের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য সরকার কয়েকটি আইন চালু করলেও কৃষকদের দুঃখদুর্দশার অবসান হয়নি। বাধ্য হয়ে কৃষকরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহোর পথে অগ্রসর হত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে প্রজাদের স্বার্থ সুরক্ষা করার কিছুটা চেষ্টা করা হয়। তাই হোমস লিখেছেন—“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল একটি দুঃখজনক ভুল।”