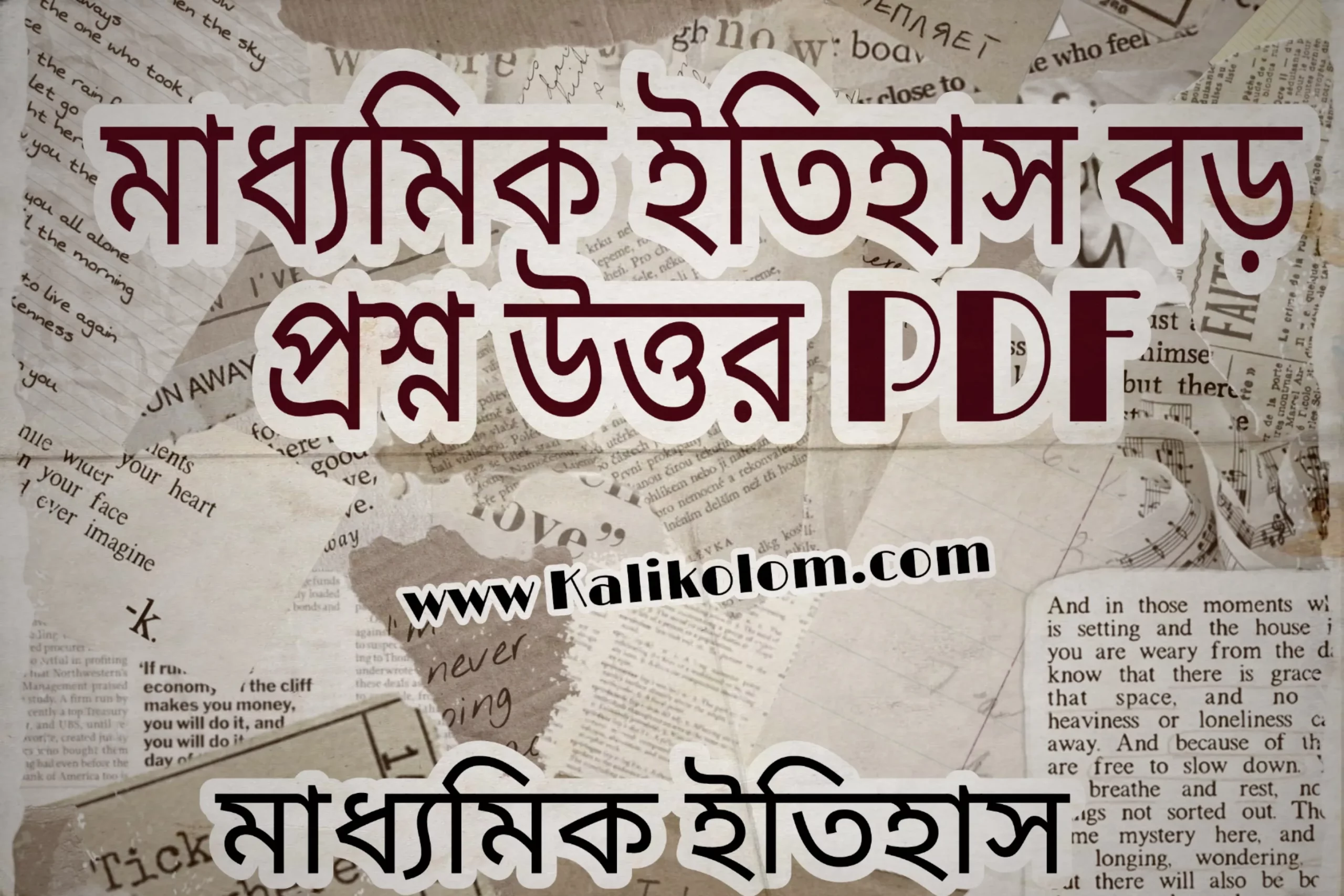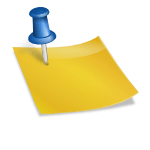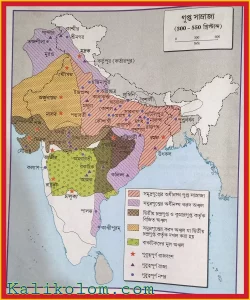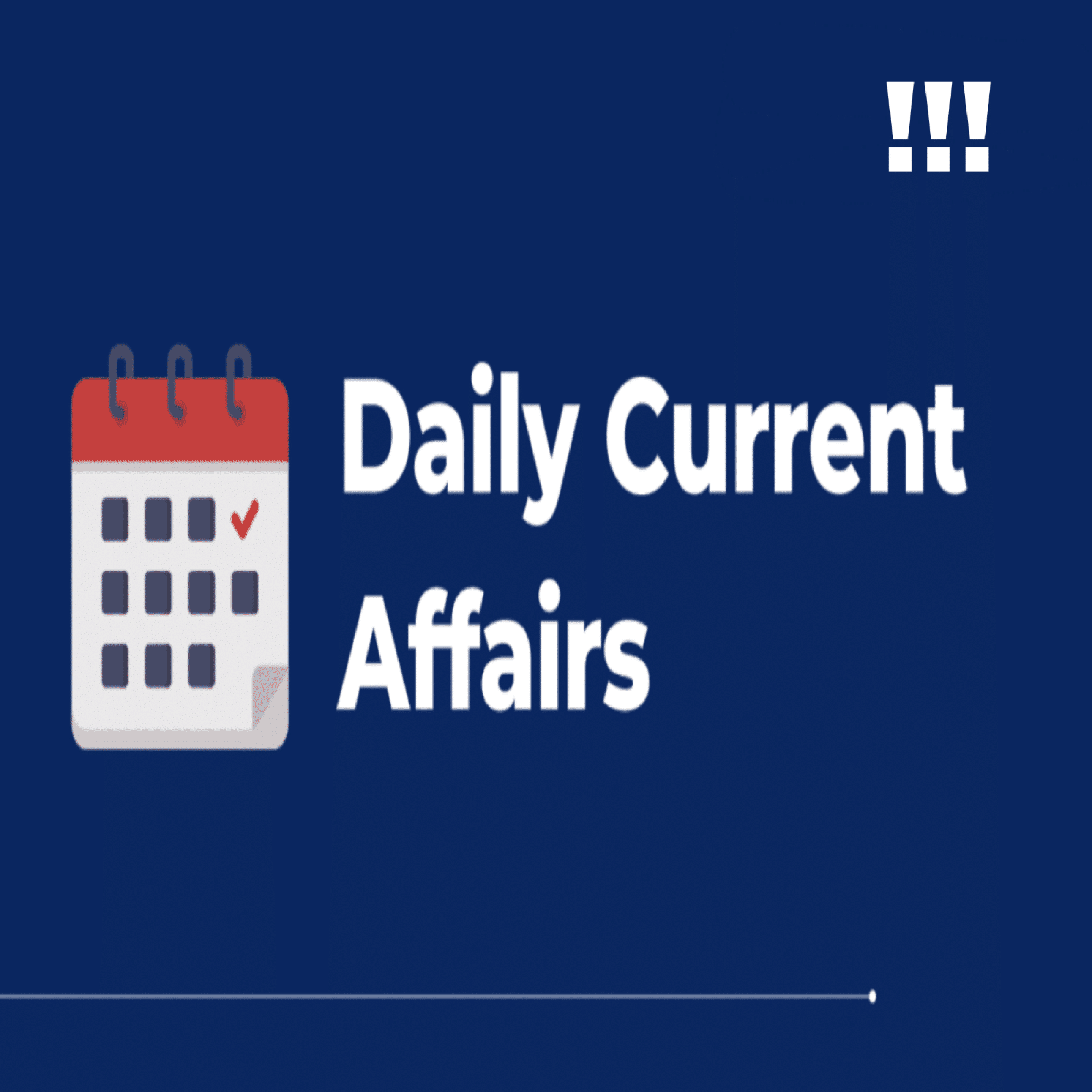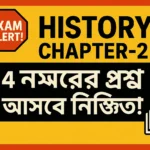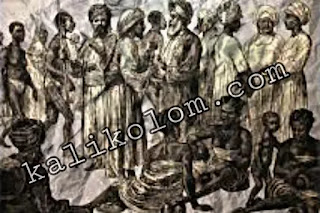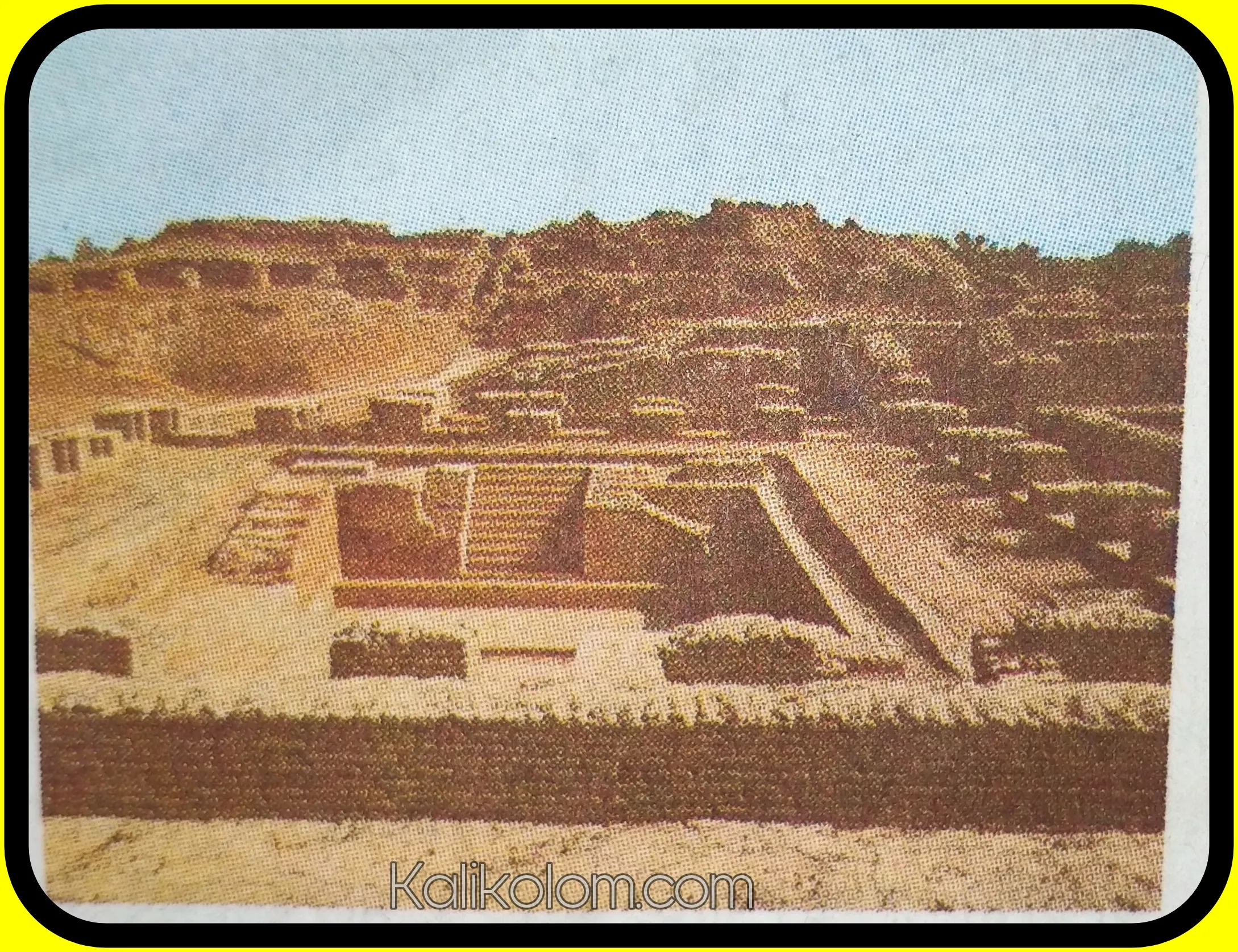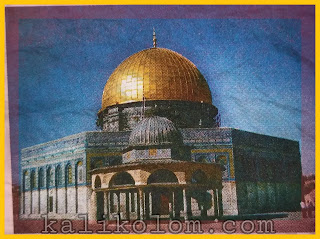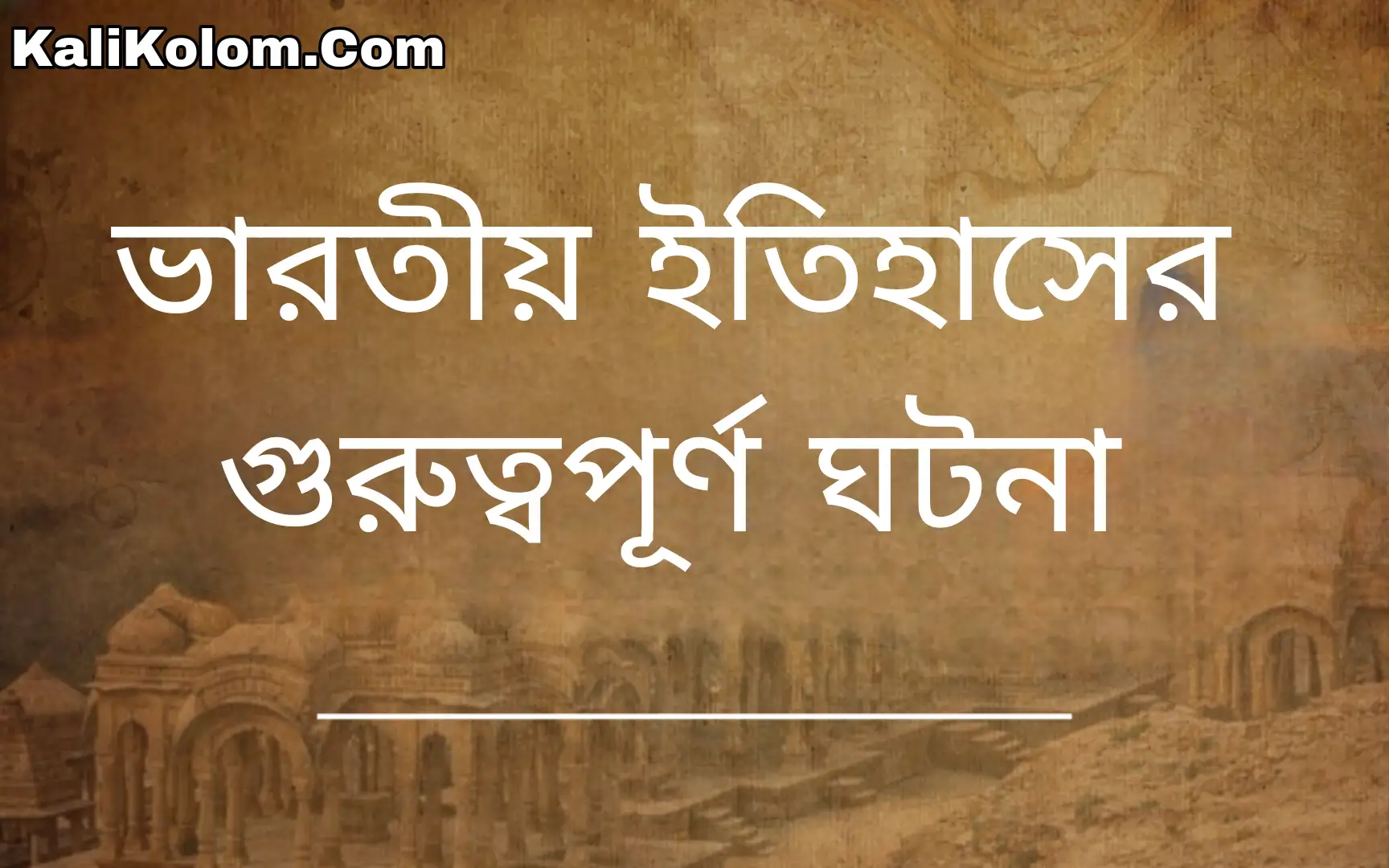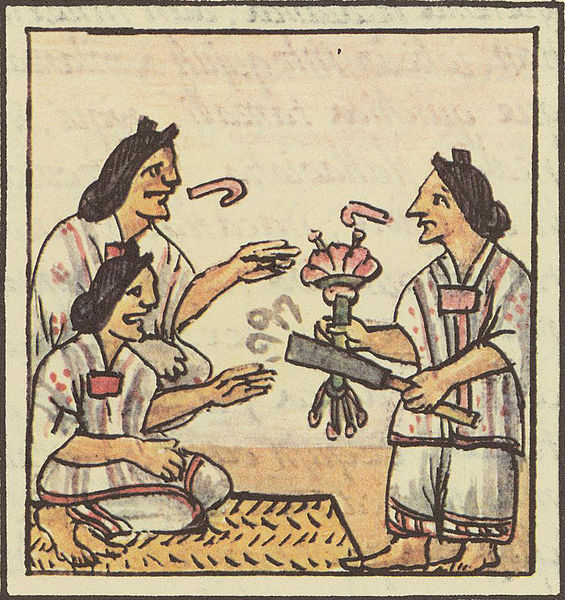বর্ণ ও জাতি
আর্যরা আজ থেকে প্রায় ৩৫০০ বছর আগে ভারতবর্ষে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসতির বিস্তার ঘটায়। ভারতে আগমনকালে আর্য সমাজে বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব ছিল কি না, য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়।
প্রাক বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা :- কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রাক্ বৈদিক যুগেও আর্য সমাজে বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। অধ্যাপক সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘ভারতে বর্ণ বৈষম্যের সূচনা, ঋক্ বৈদিক যুগের পূর্বে, আর্য ইতিহাসের ইন্দো-ইরানীয় পর্বে হয়েছিল।’
বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথা :- অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন যে, আর্যদের ভারতে আগমনকালে বৈদিক সমাজব্যবস্থায় কোনো ধরনের বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীকালে ভারতের অভ্যন্তরভাগে ‘সপ্তসিন্ধু’’ অঞ্চলে তাদের বসতির প্রসার ঘটলে গৌরবর্ণ আর্যরা ভারতের কৃয়কার অনার্যদের থেকে নিজেদের পৃথক রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভ করে। এই প্রয়োজন থেকে আর্য বা বৈদিক সমাজে বিভিন্ন পেশা বা বৃত্তির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকেই বৈদিক সমাজে বর্ণ বা বর্ণভেদপ্রথার উদ্ভব হয়। ভারতে বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় বর্ণভেদপ্রথার অস্তিত্ব থাকলেও সে যুগে জাতিভেদপ্রথার অস্তিত্ব ছিল কি না, তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক আছে।
‘সপ্তসিন্ধু‘ অঞ্চল বলতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাতটি নদী অববাহিকাকে বোঝায়। এই নদীগুলি হল— [1] শতদ্রু, [2] বিপাশা, [3] বিতস্তা, [4] চন্দ্রভাগা, [5] ইরাবতী, [6] সিন্ধু ও [7] সরস্বতী।
ভারতে বর্ণপ্রথার উদ্ভব
আর্য সমাজে বর্ণপ্রথা উদ্ভবের পেছনে কিছু কারণ ছিল। 1. আর্যজাতির মৌলিকত্ব বজায় রাখা :- গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় আর্যরা কৃত্স্নবর্ণ ও খর্বকায় অনার্যদের হীন বা নিকৃষ্ট বলে মনে করত। এই নিকৃষ্ট অনার্যদের থেকে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ও মৌলিকত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনেই বর্ণপ্রথার সূচনা হয়েছিল। ঐতিহাসিক র্যাপসন বলেছেন যে, ‘আর্য সমাজে ‘বর্ণ’ শব্দটি গায়ের রং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর্যদের গৌরবর্ণ ও অনার্যদের কৃয়বর্ণের পার্থক্য বজায় রাখতে আর্যরা তাদের সমাজে বর্ণভেদপ্রথা চালু করে।’ ঐতিহাসিক সেনার্ট মনে করেন যে, বৈদিক যুগের ‘গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য’ থেকে আর্য সমাজে বর্ণভেদপ্রথার প্রচলন ঘটেছে। শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা :- অনার্যদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংঘর্ষের মাধ্যমে আর্যরা ভারতের অভ্যন্তরে বসতির প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। সারাদিন সংঘর্ষ বা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার ফলে কোনো একক আর্য পুরুষের পক্ষে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজে নিযুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে সমাজে বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজন ও বিভিন্ন পেশার সূত্রপাত ঘটে।
চতুৰ্বর্ণ প্রথা :- বৈদিক সমাজব্যবস্থায় পেশাগত ভিত্তিতে 1. ব্রাহ্মণ, 2. ক্ষত্রিয়, 3. বৈশ্য ও 4.শূদ্র—এই চারটি পৃথক বর্ণের সূচনা হয়। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ ঋগবেদের দ্বারা এই বর্ণপ্রথা স্বীকৃত হয়। ঋগবেদের দশম মণ্ডলের পুরুষসূত্রের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, আদি পুরুষ ব্রহ্মার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, ঊরুদেশ থেকে বৈশ্য ও চরণযুগল থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। এভাবে আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি পৃথক বর্ণের সৃষ্টির কথা জানা যায়। আর্যরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিনটি বর্ণে বিভক্ত হয় এবং অনার্যরা শূদ্র বলে পরিচিত হয়। উৎপত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদের স্থান সবার উপরে এবং শূদ্রদের স্থান সবার নীচে ছিল। অবশ্য চতুর্বর্ণ কাঠামোর বাইরেও বহু অস্পৃশ্য মানুষ বাস করত। তারা মুচির পেশা, মেথরের পেশা এবং অন্যান্য নিম্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল। এরা সমাজের পঞ্চম শ্রেণি বলে পরিচিত হত।
1. চতুর্বর্ণের পেশা : আর্যদের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থায় প্রতিটি বর্ণের জন্য পৃথক পৃথক পেশা সুনির্দিষ্ট করা হয়। 1. ব্রাহ্মণ :- বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল যাগযজ্ঞ, পূজার্চনা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করা, 2. ক্ষত্রিয় :- ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করা, ¬ বৈশ্য : বৈশ্যদের কাজ ছিল ব্যাবসাবাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন করা এবং 3:- শূদ্র:- শূদ্রদের কাজ ছিল উপরোক্ত তিন শ্রেণির সেবা করা। ভৃত্য, কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকরা ছিল শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা উপবীত ধারণ করতেন এবং এই সংস্কারকে তাদের দ্বিতীয় জন্ম বলে মনে করা হত। এজন্য তারা ‘দ্বিজ’ নামে পরিচিত।
[su_divider top=”no” divider_color=”#171212″ link_color=”#161010″ size=”2″ margin=”5″]
ভারতে জাতিপ্রথার উদ্ভব সম্পর্কে বির্তক
প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণাঙ্গ অনার্যদের থেকে নিজেদের প্রভেদ বজায় রাখার জন্য বৈদিক সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র—এই চতুর্বর্ণপ্রথার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বৈদিক সমাজে আরও বিভিন্ন ধরনের পেশার সৃষ্টি হয় এবং নতুন পেশাগুলিতে বহু মানুষ যুক্ত হয়। এ ছাড়াও, কালের নিয়মেই পূর্বতন চতুর্বর্ণপ্রথায় নানা সংমিশ্রণ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন নতুন মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হয়। এই বর্ণপ্রথা থেকেই ক্রমে জাতিপ্রথার উত্থান ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঋগ্বৈদিক যুগে বর্ণপ্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিতর্ক না থাকলেও এই সময় ভারতে জাতিপ্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।
1. জাতি ব্যবস্থার সূচনা ঋবৈদিক যুগে
কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, ঋবৈদিক যুগের শুরু থেকেই আর্য সমাজে জাতিভেদপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। তাদের মতে, ঋগবেদের পুরুষসুত্বে বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চারটি জাতির উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। তাদের মতে, কর্ম বা পেশার ভিত্তিতে নয়, আর্য সমাজে জন্মসূত্রেই বর্ণ বা জাতির অবস্থান সুনির্দিষ্ট হয়। কেন না, কোনো একজন বৈশ্যের উত্তরপুরুষ অন্য পেশা গ্রহণ করলেও জন্মগতভাবে সে বৈশ্য বলেই বিবেচিত হয়। এই বিচারে, স্বগ্বৈদিক যুগের চারটি বর্ণ প্রকৃতপক্ষে জন্মসূত্রে চারটি জাতি হয়ে ওঠে। এই চারটি জাতি থেকে পরবর্তীকালে আরও বহু জাতির সৃষ্টি হয়।
2. জাতি ব্যবস্থার সূচনা পরবর্তী-বৈদিক যুগে
কোনো কোনো ইতিহাসবিদ পুরুষসুক্তের সৃষ্টিতত্ত্বকে অলীক কল্পনা আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, বৈদিক সমাজে জাতিভেদপ্রথার প্রচলন ঘটেছিল আরও পরে। তাঁদের মতে, সামাজিক সম্পর্ক:- ঋগ্বৈদিক যুগে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিল, তাদের মধ্যে মেলামেশায় বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। পেশা বংশানুক্রমিক ছিল না:- তা ছাড়া, যে পেশার ভিত্তিতে আর্যদের বর্ণ নির্ধারিত হয়েছিল সেই পেশাও বংশানুক্রমিক ছিল না। তাই ড. এ. এল. বাসাম মনে করেন যে, ঋগ্বৈদিক যুগের সমাজে শ্রেণি-বৈষম্য থাকলেও জাতি-বৈষম্য ছিল না। নেশন-এর ধারণা অনুপস্থিত:- প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কালে ‘নেশন’ (Nation) বলতে যে জাতিগত ধারণাকে বোঝানো হয় তার অস্তিত্ব ঋগ্বৈদিক যুগে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বর্ণ ও জাতিপ্রথার যোগসূত্র:- কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলাই যায় যে, বর্ণ ও জাতিপ্রথার মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র বর্তমান এবং জাতিভেদপ্রথার উদ্ভবে বর্ণপ্রথার যথেষ্ট অবদান ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে পূর্ব ভারতে আর্য বসতির প্রসার ঘটতে থাকলে সমাজে নানা জটিলতা দেখা দেয়। তখনই অর্থাৎ যজুর্বেদের যুগে সমাজে জাতিভেদপ্রথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন।
[su_divider top=”no” divider_color=”#171212″ link_color=”#161010″ size=”2″ margin=”5″]
জাতিভেদপ্রথার উদ্ভবের উপাদান
প্রাচীন ভারতে কোন্ কোন্ উপাদান বা বিষয়গুলি জাতিপ্রথার উদ্ভবে সহায়তা করেছিল সে সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।
- বর্ণপ্রথার ভূমিকা : ভারতে জাতিভেদপ্রথার উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ঋগ্বৈদিক সমাজে পেশাগত ভিত্তিতে যে বর্ণপ্রথার উদ্ভব ঘটেছিল পরবর্তীকালে তা থেকেই জাতিভেদপ্রথার উদ্ভব ঘটে। ঐতিহাসিক ড. ডি. ডি. কোশাম্বী মনে করেন যে, ঋগ্বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে আর্য সমাজের বিভিন্ন উপজাতিগুলি ভেঙে পড়তে থাকে এবং তখনই জাতিভেদপ্রথার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে, আর্যদের “এই চতুর্বর্ণ প্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষে এই চতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কৌম ছিল। প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কৌমের ভিতরে আবার ছিল অসংখ্য স্তর, উপস্তর।” এসব স্তর, উপস্তর থেকেই ভারতে জাতিপ্রথার উদ্ভব ঘটে।
- রিজলের অভিমত : হার্বাট রিজলে ভারতে জাতিভেদপ্রথার উদ্ভবে কয়েকটি সহায়ক উপাদানের উল্লেখ করেছেন, যার কোনো-না-কোনো উপাদান জাতি গঠনে সহায়তা করেছিল। উপাদানগুলি হল—
- [i] নির্দিষ্ট পেশার ভিত্তিতে কোনো উপজাতি বা তার অংশবিশেষের জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ,
- [ii] বংশানুক্রমিক পেশার পরিবর্তন করে জাতির পরিবর্তন,
- [iii] ধর্মের ভিত্তিতে জাতি নির্ধারণ,
- [iv] ভাষার ভিত্তিতে জাতির নির্ধারণ প্রভৃতি।